ডগমাটিজম: নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের প্রেতছায়া
মানব ইতিহাসের গভীর স্তরে এক ভয়াবহ ছায়া বরাবরই উপস্থিত থেকেছে—একটি বদ্ধ বিশ্বাস, এক ধরনের আত্মবিশ্বাসের অন্ধতা, যা মানুষকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে বাধ্য করেছে। এই মানসিক অবস্থানকেই বলা হয় ডগমাটিজম। এটি এমন এক মানসিক রূঢ়তা, যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো মতবাদ, ধর্ম, আদর্শ কিংবা তাত্ত্বিক কাঠামোকে একমাত্র সত্য বলে ধরে নেয়, এবং তা নিয়ে আলোচনার কিংবা সংশয়ের অবকাশ রাখে না। অথচ, সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম নিয়ামক ছিল চিন্তার স্বাধীনতা, মতের ভিন্নতা, যুক্তির ওপর বিশ্বাস। সেখানেই ডগমাটিজম হয়ে দাঁড়ায় মানব ইতিহাসের এক ভয়ংকর প্রতিবন্ধক।
ডগমাটিজম (Dogmatism)-এর ইতিহাস মূলত প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক বিতর্ক থেকে উদ্ভূত। শব্দটি গ্রিক “dogma” (δόγμα) থেকে এসেছে, যার অর্থ একটি স্থির বিশ্বাস বা মতবাদ। প্রাচীন দার্শনিকরা মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত ছিলেন: একদল ছিল “Dogmatists” — যারা কোনো সত্য বা নীতি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করতেন; অন্যদিকে ছিল “Skeptics” — যারা প্রতিটি ধারণাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।
মধ্যযুগে, বিশেষ করে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে, ডগমাটিজম আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাথলিক চার্চ বিশেষ কিছু বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীত করে তোলে (যেমন: “পোপ নির্ভুল” মতবাদ)। এই সময় ডগমাটিজম হয়ে ওঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রক্ষার একটি হাতিয়ার।
ডগমাটিজমের প্রভাব সবচেয়ে ভয়াবহ রূপে দেখা দেয় ধর্মীয় ইতিহাসে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ ছিল ডগমাটিজমের প্রতীক। চার্চের নীতিমালাকে চ্যালেঞ্জ করা মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ। বাইবেলকে যারা আক্ষরিক সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল, তারা কোনো মতবিরোধ বরদাশত করত না। গ্যালিলিও গ্যালিলির কাহিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত—তিনি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, কিন্তু চার্চের ‘পবিত্র’ বিশ্বাস ভেঙে ফেলায় তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। বিজ্ঞান আর ধর্মের দ্বন্দ্ব তখন মূলত ডগমাটিজম বনাম যুক্তিবাদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল।
ঠিক অপর দিকে ট্রফিম লিসেনকোর ভুল তত্ত্ব কমিউনিস্ট আদর্শে খাপ খায় বলে সোভিয়েত সরকার তা সমর্থন করেছিল, যদিও বিজ্ঞানীরা বিরোধিতা করেছিল। ফলে একটা সময় পরে কৃষিক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় নেমে আসে।
যখন কমিউনিজম হয়ে ওঠে একটি ‘অমোচনীয় সত্য’।
কমিউনিজম আদর্শিকভাবে মানবমুক্তির কথা বললেও, যখন কেউ এটি একমাত্র পথ বলে মেনে নেয় — যে “কমিউনিজমই চূড়ান্ত সত্য, একে প্রশ্ন করা যাবে না”, তখন এটি ডগমাটিজমে পরিণত হয়।
তার জলজ্যান্ত উদাহরণ-
সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবাদ,
চীনে মাওবাদ,
কম্বোডিয়ায় পল পটের গণহত্যা ইত্যাদি।
এইসব জায়গায় ‘শ্রমিকের শাসন’ নাম করে বাস্তবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, সেন্সরশিপ, মত প্রকাশে বাধা, ও একনায়কতন্ত্র দেখা গেছে।
আম্বেদকর মনে করতেন কমিউনিজম বাহ্যিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণ দূর করতে চায়, প্রলেতারিয়েতের শাসন প্রতিষ্ঠা করে — কিন্তু তার পথে সহিংসতা, কর্তৃত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অবমূল্যায়ন রয়েছে। তাই হয়তো তিনি
“বুদ্ধ অর কার্ল মার্ক্স” বইতে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন?
can the communist say that in achieving their valuable end they have not destroyed other valuable ends?
The end of dictatorship is to make the revolution a permanent revolution.This is a valuable end . but can the Communist say that in achieving this end they have not destroyed other valuable ends?
কিংবা কখনো বলছেন –
❝ The root cause of inequality is not just capital—it is mindset. Buddhism changes the mind. ❞
এছাড়া,
ইউরোপের ইনকুইজিশন (Inquisition) – বিশেষত স্পেন (১৫শ–১৯শ শতক)
ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলাকে ‘heresy’ বলে গণ্য করা হতো। হাজার হাজার মানুষকে অত্যাচার, বন্দি ও হত্যার শিকার হতে হয় শুধু বিশ্বাসে ভিন্নতা দেখানোর জন্য।
আফগানিস্তানের তালিবানি শাসন :
শরিয়া আইনকে একমাত্র বৈধ আইন বলে ধরে নিয়ে শিক্ষা, নারীর অধিকার, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের মতো বিষয়কে নিষিদ্ধ করে। নারীশিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা এটির একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।
ইরানের ইসলামিক রিপাবলিক:
১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই সরকার শিয়া ইসলামিক আইনের বাইরে কিছু মেনে নেয় না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করা হয়, এবং ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা বা মতবাদকে কঠোরভাবে দমন করা হয়।
এগুলো এক একটি ধর্মীয় ডগমাটিজম এর ছাপ ছাড়া আর বোধহয় কিছুই না।
আর আধুনিক তথ্যের যুগে ডগমাটিজম এক নয়া ফাঁদ, ফেক নিউজ এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারটা আজকের সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক বিষয়। যেমন QAnon বা anti-vax আন্দোলনগুলো দেখায় কিভাবে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে।
তথ্যপ্রযুক্তির যুগে, যেখানে তথ্যের প্রবাহ খুব দ্রুত, সেখানে অনেকেই যে কোনো দলের, নেতার বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ভুল তথ্যকেই সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করে নেয়।
এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার ইকো চেম্বার ডগমাটিজমের এক আধুনিক প্রতিচ্ছবি।
আলগোরিদমিক ফিল্টার বুদবুদের মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজেদের মতের সঙ্গে মেলে এমন তথ্য দেখে, ভিন্ন মত শুনতেই চায় না। এতে ডগমাটিজম আরও বদ্ধমূল হয়।
এই ডগমাটিক মনোভাব শুধু ধর্মেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাজনীতি ও রাষ্ট্রচর্চায়ও এর প্রভাব মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ এবং পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপে এক ধরনের মতবাদের একনায়কত্ব দেখা যায়, যা ডগমাটিজমেরই বহিঃপ্রকাশ। হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিন প্রমুখের শাসনামলে ‘রাষ্ট্রের সত্য’ প্রশ্নবিদ্ধ করলেই মানুষ নিঃশেষ হতো। মতবিরোধ মানেই বিশ্বাসঘাতকতা—এমন অবস্থান ডগমাটিজমকে রূপ দেয় রাজনৈতিক নির্যাতনের অস্ত্রে।
★আমার ভারত ও ডগমাটিজম :
ভারতের প্রেক্ষাপটে ডগমাটিজমের ইতিহাস আরও জটিল ও বহুমাত্রিক। প্রাচীন ভারতে দর্শনের চর্চা ছিল অত্যন্ত মুক্ত ও গণতান্ত্রিক। বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, যোগ, বৌদ্ধ, জৈন, এমনকি চার্বাকদের মতবাদও স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ বেদকে চূড়ান্ত ও অপ্রশ্ননীয় বলে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই ডগমাটিজমের শুরু। বর্ণব্যবস্থার মত একটি অমানবিক কাঠামোকে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বলে চালানো হয়, যা মানুষকে জন্মসূত্রে শ্রেণিবদ্ধ করে দেয়। ধর্ম হয়ে ওঠে একটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র।
ভারতে মুসলিম শাসন ও ঔপনিবেশিক যুগেও ডগমাটিজম নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রিটিশদের ‘White Man’s Burden’ তত্ত্ব ছিল এক ধরনের ঔপনিবেশিক ডগমাটিজম। তারা নিজেদের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শাসনব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে উপনিবেশ স্থাপনকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রচার করেছিল। অপরদিকে ভারতীয় সমাজেও এই সময় ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাত কেন্দ্রিক গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার আরও গভীর হয়। এর ফলে সমাজে যুক্তির জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়ে।
স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতেও ডগমাটিজমের ছাপ স্পষ্ট। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে অন্ধভাবে অনুসরণ, বিরোধীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা, এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য দাবি করা—সবই ডগমাটিক চেতনার ফল। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দলভিত্তিক চিন্তার একচেটিয়াবাদ, সামাজিক মিডিয়ায় একমুখী তথ্যপ্রবাহ—এই সবকিছু আজকের ভারতকে একটি উদ্বেগজনক ডগমাটিক সমাজে রূপ দিচ্ছে।
সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই প্রশ্নের উত্তরেই: আমরা কি যুক্তিবোধের আলোতে সত্যের দিকে এগোবো, না কি অন্ধ ডগমার গুহায় ফিরে যাবো ❓❓
তথ্যসূত্র :
B.R. Ambedkar – Wikiquote,
The Indian Express – Article on Ambedkar, Buddhism &Marxism,
The Buddha and His Dhamma – by B.R. Ambedkar,
Stanford Encyclopedia of Philosophy – Entry on Dogmatism,
Digital Echo Chambers and Algorithmic Bias – Harvard Kennedy School,
The Open Society and Its Enemies – by Karl Popper (Reference),
The Demon-Haunted World – Carl Sagan (Science & Anti-dogmatism)
ইত্যাদি ।
বিদ্র : গোটা আলোচনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, কারো কোনো প্রকার বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও নয় ।
উল্লেখিত আলোচনায় কোথাও কোনো তথ্য ভুল থাকলে তা প্রমান সহ সরাসরি জানাতে এবং প্রকাশ্যে তাহার সমালোচনা করতে পারেন।

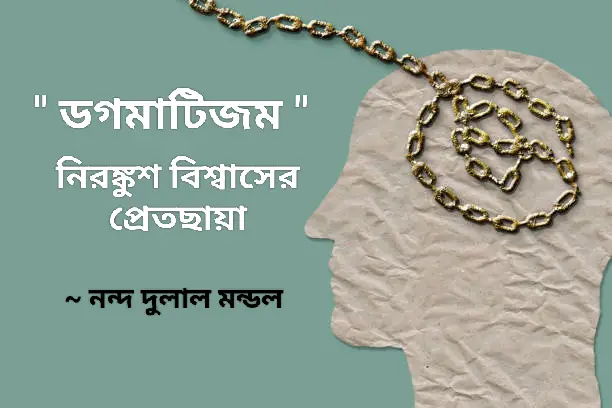

মন্তব্য করতে ক্লিক করুন